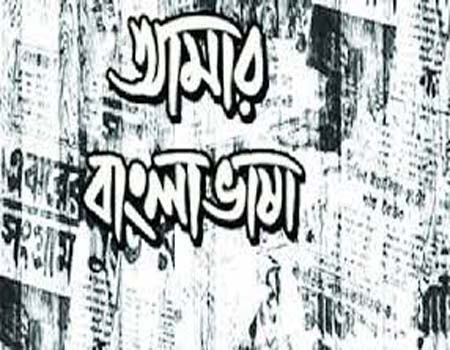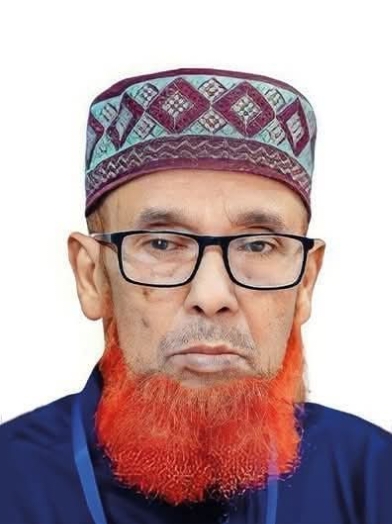আমাদের প্রিয় বাংলা ভাষা -ড. মোজাফফর হোসেন

- আপডেট সময় : ০৯:২৫:৫০ পূর্বাহ্ন, বুধবার, ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০২২
- / 309
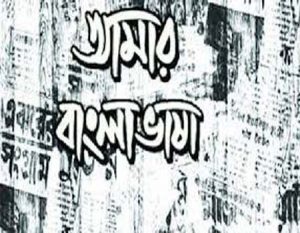
ভাষা কী
মানুষের কণ্ঠ থেকে যে ধ্বনি (Sound) বের হয়; সেই ধ্বনির যদি অর্থ থাকে, তবে ভাষা হয়। অর্থাৎ অর্থবোধক ধ্বনি সমষ্টিকে ভাষা বলা হয়। ধ্বনি হলো ভাষার প্রাণ আর বর্ণ তার দেহ। বর্ণকে ধ্বনি প্রকাশের চিহ্নও বলা হয়। ছাপাখানা তৈরি হবার আগ পর্যন্ত বাংলা ধ্বনির দেহ গঠন করা যায়নি। ছাপাখানা তৈরির পর ধ্বনির দেহ প্রকাশ পেলো। ভাষার আরেকটি নাম কথা। মুখ দিয়ে কথা বলতে গেলে ধ্বনির দরকার হয়। কথা লিখে প্রকাশ করতে গেলে বর্ণের দরকার হয়। এজন্য ভাষার দু’টি রূপ। একটি কথ্য। অন্যটি লেখ্য। যারা লেখাপড়া জানে তারা ভাষার দু’টি রূপই জানে। আর যারা লেখাপড়া জানে না তারা শুধু কথ্যরূপটা জানে। ভাষা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। ভাষা শুধু মানুষেরই হয়। পশুদের ভাষা নেই। পশু-পাখিরা কেবল শব্দ করতে পারে। তাদের সেসব শব্দের অর্থ হয় না। অর্থ না হলে ভাষাও হয় না। ভাষা না থাকার কারণে পশু-পাখিদের সুখ-দুঃখের কথা জানা যায় না। সে জন্য নিজেকে বোঝাতে এবং অন্যকে বুঝতে ভাষার গুরুত্ব বেশি। ভাষা এক একটি মানুষের অহঙ্কার। এই অহঙ্কার সম্মানের।
মানুষ যেভাবে ভাষা শিখলো
সাধারণত মানুষ মায়ের কাছ থেকে ভাষা শেখে। তাহলে মায়েরা কীভাবে ভাষা শিখল? মায়েরা কীভাবে ভাষা শিখল, তা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। সেসব গবেষণায় বলা হলো, আগে পৃথিবীতে মানুষ এসেছে, তার বহু বছর পরে মানুষ ভাষা শিখেছে। মায়েরাও তো মানুষ। অর্থাৎ মানুষ আবির্ভাবের বহুকাল পরে ভাষা সৃষ্টি হয়েছে। গবেষকদের মনে হয়েছে, প্রাচীন মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করতো বিভিন্ন উপায়ে যেমন- ইশারা বা সঙ্কেত দিয়ে, অর্থহীন অস্ফুট ধ্বনি দিয়ে, নানা রকম রেখা দিয়ে, নকশা ও চিত্র অঙ্কন করে। বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী ম্যাক্সমুলারের মতে, ইশারা-ইঙ্গিতের পরই এসেছিল মুখের ভাষা। ভাষা সৃষ্টির ব্যাপারে যেসব কথা বলা হয়েছে, তাতে কোনোভাবেই ভাষার জন্মকথা বিশ্বাসযোগ্য হয় না। The Bow-Wow Theory মতে জীবজন্তুর ডাক অনুকরণ করা থেকে ভাষার সূচনা হয়েছে। The Pooh- Pooh Theory বলছে, মানুষ আঘাত অনুভব করতে পারতো এবং সেই অনুভবের প্রকাশ থেকেই ভাষার জন্ম হয়েছে। ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে Ding-Dong Theory-তে বলা হয়েছে, মনের আবেগ প্রকাশ করতে গিয়ে যে আওয়াজ হয়েছে, তা থেকে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীন মানুষ চোখের সামনে এক একটি বস্তু দেখে বিচিত্র শব্দ করেছে আর সেসব শব্দ থেকেই ভাষার জন্ম হয়েছে। Yo-he-ho Theory-র ধারণা; মানুষ তার মনের অবসাদ দূর করার জন্য এক ধরনের শব্দ করে থাকে যেমন- কুলি-মজুরের শব্দ ‘হেইয়ো’, হুঁ হুঁ; এ থেকেও ভাষার উৎপত্তি হতে পারে। আবার Ta- ta Theory মতে মানুষ হাতের তালি বাজাতে গিয়ে ‘তা তা’, ‘তাই তাই’ শব্দ করতে পারে; এভাবেও ভাষার জন্ম হতে পারে। ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে এসব কথার ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় না। ভাষাবিজ্ঞানীরা এখন বলছেন; ভাষা কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে তার সঠিক তথ্য এখন আর পাওয়া সম্ভব নয়। তবে ভাষার উৎপত্তি নিয়ে পবিত্র কুরআনের একটি বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা রহমানে বলা হয়েছে- ‘তিনি (আল্লাহ) মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে (মানুষকে) ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন’ (আয়াত : ২-৩)। পবিত্র কুরআনের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে- ‘হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও’ (সূরা হুজরাত : ১৩)। পবিত্র কুরআনের এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, মানুষ ভাষা শিখেই পৃথিবীতে এসেছে। কাজেই পৃথিবীতে আগে মানুষ এসেছে এবং পরে ভাষা সৃষ্টি হয়েছে, এ কথা আর বলা যায় না। পৃথিবীতে যে দু’জন মানুষ (আদম আ. ও হাওয়া আ.) প্রথম এসেছেন, তাঁদের ভাষা ছিল আরবি। আদম আ. ও হাওয়া আ.-এর ছেলে-মেয়ে থেকেই ধ্বনি তারতম্যে বিভিন্ন ভাষার (প্রায় সাড়ে চার হাজার) জন্ম হয়েছে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানও বলছে, পৃথিবীর প্রধান প্রধান বিশ-বাইশটি ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর সদস্য। কুরআনের বক্তব্য থেকে বলা যেতে পারে, পৃথিবীর প্রধান ভাষাসমূহ একটি ভাষা থেকেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করেছে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা কুরআনের বক্তব্যকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে পারেনি। নতুন করে গবেষণা হলে কুরআনের বক্তব্য সঠিক বলে প্রমাণিত হবে।
বাংলা ভাষার জন্ম হলো যেভাবে
পৃথিবীতে ভাষাগোষ্ঠী আছে। ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষাগোষ্ঠীর সদস্য। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর দুটি শাখা, একটি ‘কেন্তুম্’; অন্যটি ‘শতম’্। শতম্ এর কয়েকটি শাখা রয়েছে; তার মধ্যে ভারতীয় শাখা। ভারতীয় ভাষার একটি রূপ প্রাকৃত। প্রাকৃত থেকে মাগধি, তার থেকে ওড়িয়া; অসমিয়া; বিহারি; বাংলা। অর্থাৎ ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। সেখান থেকে প্রাকৃত, মাগধি হয়ে বাংলা ভাষার জন্ম।
বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শন চর্যাগীতিকা। চর্যাগীতিকা যে ভাষাতে লেখা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সে ভাষাকে বাংলা বলেছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমাণ করেছেন যে, চর্যাগীতিকার ভাষা ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যকার ভাষা। এ সময়ের পূর্বে বাংলা ভাষার রূপ কেমন ছিল তা জানা যায়নি। তবে এ সময়ের পূর্বেও বাংলা ভাষা ছিল।
বাংলা যেভাবে আমাদের মাতৃভাষা হলো
কবি কায়কোবাদ তাঁর ‘বঙ্গভূমি ও বঙ্গভাষা’ কবিতায় বললেন-
‘বাংলা আমার মাতৃভাষা বাংলা আমার জন্মভূমি
গঙ্গা পদ্মা যাচ্ছে বয়ে যাহার চরণ চুমি।
ব্রহ্মপুত্র গেয়ে বেড়ায় যাহার পুণ্য-গাথা!
সেই সে আমার জন্মভূমি, সেই সে আমার মাতা’।
কবির দেশমাতা আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশ। যার আদি নাম ছিল বঙ্গ। প্রাচীনকালে বঙ্গে যে জাতি বাস করতো তাদেরকে বলা হতো বোঙ্গা। এই বোঙ্গা শব্দ থেকে কালক্রমে বাংলা হয়েছে। বোঙ্গা হয়তো তাদের ভাষার নাম ছিল। পৃথিবীতে অনেক জাতির নামকরণ করা হয়েছে, তাদের ভাষার নামে। ভাষার নামের সাথে মিল রেখে আমাদেরকেও বাঙালি বলা হয়। তাহলে আমাদের পূর্বপুরুষদের ভাষা ছিল বোঙ্গা। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে আমাদের দাদি, পরদাদিরা শিখেছেন। তাদের কাছ থেকে মা-খালারা বাংলা ভাষা শিখেছেন। যেমন- বউকে আমাদের পূর্বপুরুষরা বলতো বধূ, পরদাদিরা বলতো বহু, এখন মা-খালারা বলে বউ। এভাবেই আমাদের মায়েদের ভাষা বোঙ্গা থেকে বাংলা হয়েছে। মাতৃভাষা মানে মায়ের ভাষা। আমরাও বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে পেয়েছি। এ জন্য কবি বলেছেন-
‘মোদের গরব মোদের আশা
আ-মরি বাংলা ভাষা।
মাগো তোমার কোলে, তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালোবাসা
আ-মরি বাংলা ভাষা’।
আমাদের বাংলা ভাষা আন্দোলন
মানুষ নিজেদের প্রতি অবজ্ঞা মেনে নিতে পারে না। নিজেদের ভালোবাসাকে কেউ অবহেলা করুক সেটাও মানতে পারে না। আমরাও পারিনি। বাংলা ভাষাকে আমরা ভালোবাসি। আমাদের ভাষাকে অবহেলা করেছিল পাকিস্তান শাসকরা। এই অবহেলা থেকে শুরু হয়েছিল ভাষা আন্দোলন। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামে তৈরি হয় দু’টি দেশ। বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চল তখন পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তান দু’ভাগে পরিচিত ছিল। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান। নতুন দেশ পাকিস্তান। এ দেশের দাপ্তরিক ভাষা কী হবে, এ নিয়ে চলে আলাপ-আলোচনা। পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের মাতৃভাষা ছিল উর্দু। পূর্ব পাকিস্তানের বেশির ভাগ মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। তখন পাকিস্তানের রাজধানী ছিল করাচি। করাচি থেকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো। এ সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লিয়াকত আলী খান। পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দীন। প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীসহ উর্দুভাষী বুদ্ধিজীবীরা উর্দুভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করার প্রস্তাব করল। পূর্ব পাকিস্তান থেকে দাবি করা হলো; বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করা হোক। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের দাবি মানল না। দাবি না মেনে ঘোষণা করল; উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা। এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করল ঢাকার ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা। এর মধ্যে অন্যতম ছিল ‘তমদ্দুন মজলিস’ নামে একটি সংগঠন। আন্দোলন চলতে থাকল। প্রতিবাদ জোরালো করতে ১৯৫০ সালের ১১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠন করা হলো ‘রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’।
ভাষা আন্দোলনে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কাগজে-কলমে রাষ্ট্রভাষা থেকে বাংলাকে বাদ দেওয়ার দিন। এ দিন ঢাকাতে ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’ স্লোগানে পালিত হলো সাধারণ ধর্মঘট। ধর্মঘট চলার সময় ছাত্ররা পুলিশের রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। ছাত্রদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ বাধল। এর প্রতিবাদে ১২ মার্চ থেকে ১৫ মার্চ আবার ধর্মঘট চলল। আন্দোলন ধীরে ধীরে বেগবান হতে থাকল।
আন্দোলন থামাতে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এলেন। ঢাকা এসে তিনি বক্তৃতা করলেন। বললেন, ‘উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা’। জনসাধারণ তার এ বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করল। ১৯৫২ সালের শুরু থেকে ভাষা আন্দোলন এগোতে ছিল। এর মধ্যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন খাজা নাজিমুদ্দীন। তিনিও ঢাকায় এলেন। তিনি পল্টন ময়দানের জনসভায় বললেন- পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কেবল হবে উর্দু। সঙ্গে সঙ্গে ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’ স্লোগানে পল্টন ময়দান প্রকম্পিত হয়ে উঠল। নাজিমুদ্দীন সাহেবের বক্তব্যের প্রতিবাদে ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালিত হলো। ৩১ জানুয়ারি মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে গঠিত হলো ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’। ইতোমধ্যে পাকিস্তান সরকার আরবি হরফে বাংলা লেখা প্রস্তাব করল। এ প্রস্তাবের প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ‘রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল, জনসভা ও বিক্ষোভের ডাক দিলো। সরকার ১৪৪ ধারা জারি করল। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নিলো। ছাত্ররা ৫-৭ জনের ছোটো ছোটো গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’ স্লোগান দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। ছাত্রদের প্রতিহত করতে মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করল। লাঠি চার্জে ছাত্ররা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ছাত্রদের সামলাতে মিছিলে পুলিশ এবার গুলি চালাল। গুলিতে রফিক উদ্দিন আহমদ, আবদুল জববার, আবুল বরকত এবং আবদুস সালাম শহীদ হলেন। এজন্যই কবি আল মাহমুদ বলেছেন-
‘ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
দুপুর বেলার অক্ত
বৃষ্টি নামে বৃষ্টি কোথায়
বরকতের রক্ত’।
এসব মৃত্যুর প্রতিবাদে পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি শোকমিছিল বের করা হলে পুলিশ আবারও গুলি চালাল। সেই গুলিতে শফিউরসহ আরো কয়েকজন শহীদ হলেন। ১৯৫৬ সাল পর্যন্তু ভাষা আন্দোলন চলতে থাকে। এরপর বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য বিল পাস করা হলো। ১৯৫২ সালের পর থেকেই ২১ ফেব্রুয়ারির দিনটিকে ভাষাদিবস হিসেবে পালন করা হয়। মাতৃভাষার জন্য আত্মত্যাগ। এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেসকো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে। তখন থেকে পৃথিবীব্যাপী ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন হয়ে আসছে। আন্তর্জাতিকভাবে দিবসটি পালন করা বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য গর্বের। কেননা এ দিনে বাংলা ভাষার জন্য আত্মত্যাগের বিষয়টি এসে যায় বিশ্ববাসীর কাছে। তখন বিশ্বব্যাপী বাংলা ভাষার মর্যাদা বাড়তে থাকে। ভাষা আন্দোলনই পরে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা দিয়েছে।
বাংলা ভাষা আবারও অবহেলার শিকার
রাজনৈতিক কারণে বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করেছিল। সেই অবজ্ঞা সহ্য করতে না পেরে ‘ভাষা আন্দোলন’ করে বাংলা ভাষার মর্যাদা ফিরিয়ে এনেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলা ভাষা আবার অবহেলার শিকার হয়েছে। তখন হয়েছিল পাকিস্তানিদের মাধ্যমে। এবার হচ্ছে আমাদের নিজেদের মাধ্যমে। নিজেদের মাধ্যমে যে বাংলা ভাষা অবহেলার শিকার হয়েছে সে কথা ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের ‘বাংলাটা ঠিক আসেনা’ কবিতা থেকে বোঝা যায়। তিনি লিখেছেন-
‘ছেলে আমার খুব সিরিয়াস কথায় কথায় হাসেনা
জানেন দাদা, আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসেনা।
ইংলিশে ও ‘রাইমস’ বলে
ডিবেট করে, পড়াও চলে
আমার ছেলে খুব পজিটিভ অলীক স্বপ্নে ভাসেনা
জানেন দাদা, আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসেনা।
ইংলিশ ওর গুলে খাওয়া, ওটাই ফাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ
হিন্দি সেকেন্ড, সত্যি বলছি, হিন্দিতে ওর দারুণ তেজ।
কী লাভ বলুন বাংলা পড়ে?
বিমান ছেড়ে ঠেলায় চড়ে?
বেঙ্গলি থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ তাই, তেমন ভালোবাসেনা
জানেন দাদা, আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসেনা’।
যে মাতৃভাষার জন্য দীর্ঘ ইতিহাস, সংগ্রাম, রক্ত, আত্মত্যাগ সেই বাংলা ভাষা আজ মর্যাদা হারাতে যাচ্ছে। রাষ্ট্রের অনেক বিভাগেই এখনও বাংলা ভাষা গুরুত্বহীন। অথচ ভাষা আন্দোলনের স্লোগানই ছিল ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’। ভাষা আন্দোলনের প্রায় পঁচাত্তর বছর পার হতে চলল। এখনো আদালতে বিদেশী ভাষা রয়েই গেল। এদেশের করপোরেট অফিসগুলোতে বাংলা ভাষার মর্যাদা নেই। রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে নতুন প্রজন্মকে আকৃষ্ট করতে বিদেশী ভাষা শেখার শত শত স্কুল তৈরি হয়েছে। রাষ্ট্রের চিকিৎসা ব্যবস্থায় বাংলা ভাষা গুরুত্বহীন। রাষ্ট্রীয় দপ্তর বাংলা ভাষায় চলে না। সরকারি চাকরির পরীক্ষায় মাতৃভাষায় কথা বললে, চাকরিও সরকার দিতে চায় না। গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান, বিয়ের অনুষ্ঠান, শিক্ষাসফর, হালখাতা, জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী ইত্যাদি অনুষ্ঠানে হিন্দি ও ইংরেজি গানের আধিপত্যে বাংলা গান লজ্জায় মরে যেতে চায়। এ-ই যদি চলতে থাকে তাহলে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস গুরুত্ব ম্লান হয়ে যায়। একুশে ফেব্রুয়ারি এলে এদেশের নেতারা ভাষা আন্দোলনের অতীত বোঝাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বাংলা ভাষার হাড়ের ভেতর যে ক্ষয় ধরেছে সে রোগের চিকিৎসার দায়িত্ব কেউ গ্রহণ করতে চায় না। শুধু বক্তৃতার নাম ভাষাপ্রীতি নয়।
বাংলা ভাষা হারিয়ে গেলে বাঙালি জাতির অস্তিত্বও বিলীন হতে পারে; এ কথাটা মনে রেখে ‘রাষ্ট্রভাষার দাবিতে আমাদের শিশুরা রাজপথে আবারও নামতে পারে বৈকি!’