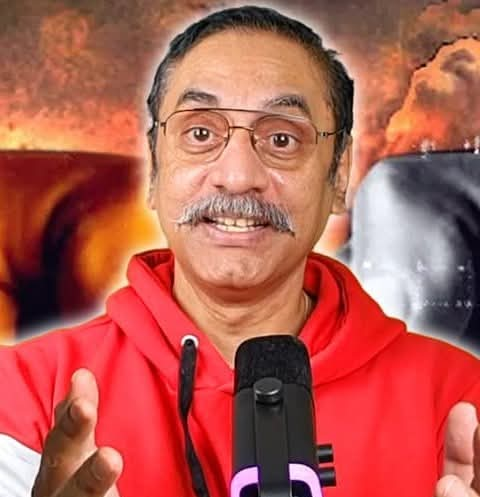ইয়াং উদীয়মান স্কলারদের উদ্দেশ্যে

- আপডেট সময় : ১০:০৭:০২ পূর্বাহ্ন, বুধবার, ৯ এপ্রিল ২০২৫
- / 174
ইংরেজরা কলকাতা-কেন্দ্রিক কিছু ব্যবসায়ী এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাবাহিনীর কিছু ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে নবাবকে পরাজিত করে (১৭৫৭)। সে সময় পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মানুষের মধ্যে আর্থ-সামাজিক অবস্থানে কোনো তফাৎ ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশরা ১৭৫৭ সালের পর কলকাতা-কেন্দ্রিক একটি নির্ভরশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি করল, যাদের উপর তাদের মৌলিক দুটি দায়িত্ব ছিলো:
প্রথম দায়িত্ব ছিল—মুসলিম শাসনের কয়েকশ বছরের প্রভাবময় অবস্থানকে শেষ করায় ব্রিটিশদের সহায়তা করা; এবং ইসলামকে পাবলিক স্পিয়ার থেকে সরিয়ে ফেলা। এই কলকাতা-ভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ব্রিটিশরা আরাম-আয়েশে রাখে ও চাকরি দিয়ে লালন-পালন করে।
মুসলিম আমলে কলকাতা নামে কোনো শহর ছিল না। এটি ছিল কেবল ব্রিটিশদের একটি ব্যবসায়িক কুঠি। ব্রিটিশরা এই শহর গড়ে তুলে এখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নিজেদের আদর্শের গায়ক বানায়। তারা নাটক, গান, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে মুসলিম বিদ্বেষমূলক দৃষ্টিভঙ্গির চর্চা করতে লাগল, কারণ ব্রিটিশ দাতারা এই ঘরানার চর্চাকে পুরস্কৃত করত।
দ্বিতীয় দায়িত্ব ছিল—পূর্ব বাংলার কৃষক-শ্রমিক শ্রেণিকে হেয় করা, বিশেষ করে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববাংলার মানুষদের। তারা পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলেও, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় যখন ঢাকা কেন্দ্রিক প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে উঠছিল, তখন নিজেরা আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কায় টেনশনে পড়ে যায়। তারা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা শুরু করে। এর মাধ্যমে স্পষ্ট একটি সাংস্কৃতিক ও শ্রেণিগত বিভাজনরেখা তৈরি হয়—যা এখনো টিকে আছে।
ভয়াবহ বিষয় হলো- পশ্চিমবাংলার এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি পূর্ববাংলায় একটি অনুরূপ শ্রেণির জন্ম দেয়। যারা কলকাতা ও তার সংস্কৃতিকে বাঙালি পরিচয়ের কেন্দ্র হিসেবে মেনে চলে। এই শ্রেণি পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতিকে একপ্রকার ধর্মীয় ভাবগাম্ভির্যের সাথে অনুসরণ করে। কিন্তু বাস্তবে এই বিভাজনরেখা ব্রিটিশদের তৈরি একটি স্থায়ী ক্ষত। যার প্রভাব থেকে পূর্ববাংলা কখনোই মুক্ত হতে পারেনি।
১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান কিছুটা স্বস্তি পেলেও, কলকাতা ভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির চাপে ব্রিটিশরা মাত্র সাত বছরের মাথায় ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিলে পশ্চিমবাংলার পক্ষ থেকে তীব্র বিরোধিতা শুরু হয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের হয়ে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের বিজয়ে পূর্ববাংলার মানুষ আশান্বিত হলেও তাকে অল্প সময়ের মধ্যেই বিতর্কিত করা হয়। এই বিভাজন রেখার কারণে পূর্ববাংলার জনগণ আলাদা রাজনৈতিক স্বতন্ত্রতার দিকে ঝুঁকে পড়ে, যার ফলাফল ছিল পাকিস্তান আন্দোলনে পূর্ববাংলার সক্রিয় অংশগ্রহণ।
কিন্তু ১৯৪৭ সালের পর এক নতুন ধারা শুরু হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে ‘বৈষম্য’ শব্দটি প্রতিষ্ঠা পায়। আসলে ১৯৪৭ সালের আগে পূর্ববাংলার সচিব, সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা বা বড় আমলা বলতে গেলে ছিল না। অথচ পাকিস্তানের উপর একতরফা দোষ চাপানো হয়।
পূর্ববাংলায় এই শূন্যতা ও বৈষম্য তৈরি হয়েছে ব্রিটিশ ও পশ্চিম বাংলার যোগসাজেশে। তারা পূর্ববাংলাকে বঞ্চিত করেছে অথচ দোষ চাপিয়ে দিয়েছে নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের উপর। ব্রিটিশ আমলে কারা পূর্ববাংলায় রাস্তাঘাট, কলকারখানা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরিতে বাধা দিয়েছে? এই প্রশ্ন আশাকরি বাংলাদেশের ইয়াং স্কলাররা করবেন।
১৯৭১ সালে দেখা যায়—যখন পশ্চিম পাকিস্তানের সেক্যুলার রাষ্ট্রযন্ত্র (ভুট্টো-ইয়াহিয়া) পূর্ববাংলায় গণহত্যা চালায়, তখন দোষারোপ করা হয় জামায়াতে ইসলামীর ওপর। অথচ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জামায়াত ৫% ভোটও পায়নি। বাস্তবতা হলো, পশ্চিম পাকিস্তানের সেক্যুলাররাও জামায়াতকে দায়ী করে মূলত ইসলামবিদ্বেষী বাঙালি গোষ্ঠিকে সন্তুষ্ট করে।
১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রকে গালাগালি করা যেভাবে চলেছে, স্বাধীনতার পর সেই একই ভাষায় জামায়াতকে আক্রমণ করা শুরু হয়। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, জামায়াত ইসলামী সহ বেশ কয়েকটি ডান ও বাম দল পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছে। কিন্তু দোষারোপ করা হয় জামায়াতকে। কারণ জামায়াত ইসলামী চিন্তাধারার সবচেয়ে দৃঢ় সংগঠন হিসেবে টিকে আছে। এখানে মূল বিষয় ইসলাম বিদ্বেষ।
১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সেকুলার শাসকরা বাঙালিদের হত্যা করলো, তার কোনো বিচার হয়নি। ১৯৭১ সালের পর এদেশের হাজার হাজার আলেম ওলামাকে হত্যা করা হয়। এর কোনো বিচার হয়নি। একটা দূর্বল দলের উপর দায় চাপিয়ে দিয়ে সবাই পার পেয়ে গেল। নিজেদের দাবীর সত্যতা প্রমাণে জামায়াত নেতাদের বিচার করতে যেয়ে পৃথিবীর অন্যতম জঘন্য বিচারের আয়োজন করল।
এবার মূল কথায় আসি। পশ্চিমবাংলা ও তাদের সহযোগী বুদ্ধিজীবিরা বরাবরই বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছে। আওয়ামী লীগ ভারতের প্রেসক্রিপশন গ্রহণ করায় তাদের বক্তব্যেও একই সুর লক্ষ্য করা যায়। জিয়াউর রহমান, খালেদা জিয়া কিংবা অন্যান্য ইসলামপন্থী নেতৃত্ব—তাদের সবাইকেই ভারত এবং কলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের রোষানলে পড়তে হয়েছে।
দিল্লিতে আমার থাকার অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে—ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মানুষ পশ্চিম বাংলার বুদ্ধিজীবীদের পছন্দ করে না। কারণ তারা শুধুমাত্র পূর্ববাংলা নয়, বরং পুরো ভারতকে নিজেদের ‘বুদ্ধিবৃত্তিক ঔপনিবেশিক মনোভাব’ দিয়ে বিচার করে। অথচ বাস্তবে পশ্চিমবাংলা আজ ভারতের অন্যতম দরিদ্র প্রদেশ, এবং সেখানে তৈরি হওয়া বুদ্ধিজীবিতার ধারা পশ্চিমবাংলার বাইরেও তেমন গ্রহণযোগ্য নয়।
বাংলাদেশে গত ৫৩ বছরে কলকাতা-কেন্দ্রিক চিন্তার ধারা প্রভাব বিস্তার করলেও, ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর ক্রমশ সেই প্রভাব হারিয়ে যাবে। বিপ্লব টিকে থাকার জন্য এর কোনো বিকল্প নাই বলেই বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।
বাংলাদেশের মানুষ এখন নিজেদের পথ খুঁজে নিতে প্রস্তুত হচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি—বাঙালি কোনো বিভাজন ছাড়াই মুসলিম আমলে একটানা সাড়ে পাঁচশ বছর ধরে পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক অঞ্চল ছিল। সেই ঐতিহ্য বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের হাত ধরে আবার ফিরে আসবে, ইনশাআল্লাহ।
আশাকরি- বাংলাদেশের স্কলাররা আর পশ্চিমবাংলার ঘৃণানির্ভর ও ইসলাম বিদ্বেষী বুদ্ধিবৃত্তিকে অনুসরণ করবে না। নিজেরা নিজেদের একাডেমিক যোগ্যতায় বিশ্বমঞ্চে নিজেদের অবস্থান তৈরি করে নিবে।
(নোট: তবে হ্যাঁ, পশ্চিম বাংলায় যারা পুরাতন ধ্যাণ ধারণা থেকে বের হতে পেরেছে, তারা বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। তারা ঘৃণাজীবি নয় এবং ধর্ম বিদ্বেষীও নয়।)